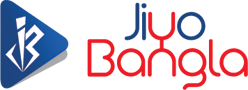মকরসংক্রান্তির ভোরে, যখন আমাদের সেই গাঁয়ের স্যাঙাৎ নদীটির বরফহিম জলে কুয়াশা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরত, তখন আমরা ‘যত ডুব, তত পিঠে’ ঘুষতে ঘুষতে নাইতে যেতাম তার বুকছ্যাচা জলে। পাড়ে দাঁড়িয়ে হু হু বাতাসের ভীষণ কাঁপুনিকে রামকলা দেখিয়ে যে একছুটে পালিয়ে আসব তারও উপায় নেই; কারণ, ভেতরে তখন ক্ষীর টসটস পিঠে খাবার দুর্নিবার লোভ—কোন এক আলপ্পেয়ে নিয়মে কম সে কম কুব কুব তিন ডুব না-দিলে নাকি পৌষ-পার্বণের পিঠেই খাওয়া যাবে না! তাই হিমের ভেতরে গা না-ডুবিয়ে আর কোন উপায় থাকে না।
দোনামনা করে ডুব দিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই এদিন পুব আকাশ ফরসা হত। পথে দেখা হত খোল-করতাল-হারমোনিয়াম নিয়ে চাদরমুড়ি দিয়ে প্রভাতফেরিতে বেরিয়ে পড়া হরিভক্তদের সঙ্গে। ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে সুর তুলে তাঁরা যেতেন একে একে গাঁয়ের সকলের বাড়ি। নামগান করে শালপাতার দোনা ভরে আস্বাদ নিতেন ‘মকর চাল’-এর। এই আস্বাদের সাধনপথে সঙ্গী হতাম আমরাও। খাঁটি গরুর দুধের সঙ্গে চালের গুঁড়ো, চিনি বা আখের গুড় জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে ক্ষীরের মতো ঘন করে তা উনুন থেকে নামানো হত। তারপর, আগে থেকে গরম জলে ভিজিয়ে রাখা আতপ চাল আর কুচনো নানান ফল সেই ক্ষীরের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি হত, ‘মকর চাল'। কনকনে শীতের সকালে গরম গরম মকর চালে শরীর ওম হত, আর, সুস্বাদে রসনা বলত--‘অপূর্ব’!
তো এদিন, স্নান সেরে একে-অপরকে মকর চাল খাইয়ে বেশ ঘটা করে ছেলেতে-ছেলেতে আর মেয়েতে-মেয়েতে পাতানো হত বন্ধুত্ব; সেই বন্ধুত্বের নাম ছিল, ‘মকর’। উনিশ শতকের কবি ঈশ্বর গুপ্ত; তাঁর ‘পৌষ-পার্বণ’ কবিতায় এই বন্ধু-নামের উল্লেখ রয়েছে :
"মকর-সংক্রান্তি-স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই চল চল চল।।"
আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে সুদূর গাঁ-গঞ্জের যেসব স্ত্রীলোক কপালগুণে এই মকর সংক্রান্তিতে জীবনে একবার গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সুযোগ পেতেন, তাঁরা স্নান করে পূণ্য অর্জনের ফাঁকে নিজেদের সঙ্গী কিম্বা তীর্থের কোন সদ্য পরিচিতের সঙ্গে ‘গঙ্গাসাগর’ পাতিয়ে এক নতুন বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতেন। গঙ্গার জলে অবগাহন করে যেমন পুন্যি হয় বলে মনে করা হয়, তেমনি একদা তার বুক-জলে নেমে শপথ নিয়ে পাতানো সই-সম্পর্কও বড় পবিত্র বলে মনে করা হত। এছাড়াও বাংলার ভাগীরথী গঙ্গার বুকে একদা পুণ্য-পার্বণ উপলক্ষে আঁজলা ভরে একে-অপরের হাতে জল দিয়ে মেয়েতে-মেয়েতে পাতানো হত আর এক সই-সম্পর্ক, ‘গঙ্গাজল’।
সেকালের সইয়েরা কিন্তু প্রায়শ নিছক আবেগের বশেই নিজেদের ছেলেমেয়ের মধ্যে বিয়ে দেবার অঙ্গীকার করে বসতেন। ছেলেমেয়েরা হয়তো তখন নেহাতই শিশু; তবুও বড় হলে বিয়ে দেবেন, দুই সইয়ের সম্পর্ক আরও পোক্ত হবে—এই ভাবনা থেকেই বোধহয় তাঁরা একে-অপরকে কথা দিয়ে বসতেন। সুখের কথা, প্রায়ই সেটা ছাদনা অব্দি গড়াত। তবুও, গ্রহের ফেরে মাঝে মাঝে বেশ বিপত্তিও ঘটত। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'দ্বিতীয় পর্বে’ ভবঘুরে শ্রীকান্তের কথাই না-হয় ধরুন। শ্রীকান্তর মা এক মহিলার সঙ্গে 'গঙ্গাজল' পাতিয়েছিলেন। তখন শ্রীকান্তর নেহাতই কিশোরবেলা। শ্রীকান্ত বড় হতে এবং দস্তুরমতো ভবঘুরে হয়ে উঠতেই তার হাতে এলো গঙ্গাজলকে লেখা মায়ের একখানা চিঠি। এই প্রসঙ্গেই জানা গেল বৃত্তান্ত :
"...বছর বারো-তেরো পূর্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এ গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সে মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর ছেলে ত আছে। তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদি একান্তই অভাব হয়, তখন আমি ত আছি!"
ভবঘুরে শ্রীকান্তের জীবনে এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা আর কী-ই বা হতে পারে, বলুন! তবে স্বস্তির কথা এই যে, মায়ের চিঠিতে ‘যদি’-র ফাঁকটুকু পেয়ে আর 'সৎপাত্র' জুটিয়ে দেবার খরচ বহন করতে চেয়ে শ্রীকান্ত সে-যাত্রা মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু, সবার কপালে তো আর ‘যদি’র ফাঁক থাকত না; ফলে, মুক্তিও জুটত না। ‘যদিদং হৃদয়ং’-জপতে জপতে শেষমেশ কথা রাখতে বাঁধা পড়তেই হত ‘উদ্বাহুবন্ধনে’!
কেতাব থেকে আবার ফিরি আমাদের গাঁয়ের কথায়। সেখানে আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে কাছেপিঠে কোন বড় রাস্তা ছিল না, বাস তো দূরের কথা—আধুনিক যুগের ছাপমারা কোন গাড়িই চলত না। বাসে চড়ে দূরে কোথাও যেতে হলে বোঁচকাবুঁচকি ঘাড়ে করে হাঁটতে হত কয়েক মাইল। এমনধারা কষ্ট করেই একবার আমার ঠাকুমা তাঁর গাঁয়ের এক জায়ের সঙ্গে পুরুষোত্তমক্ষেত্র পুরী গিয়েছিলেন। শ্রীজগন্নাথকে চোখের দেখা দেখতে। তার জন্য তিল তিল করে বহুদিন ধরে জমিয়েছিলেন একটি একটি করে টাকা। গ্রাম্যবাঙালির কাছে তখনও তীর্থ বলতে হয় মধুরা-বৃন্দাবন, নয় গঙ্গাসাগর, কিংবা পুরী। তবে, পুরী যাওয়া যতটা সহজ ছিল, অন্যত্র ততটা ছিল না। ফলে, সেখানে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করেই বাঙালি বিধবারা তখন ভারততীর্থের সাধপূরণ করতেন। সেদিন তাঁরা আজকের মতো, এত সহজে দ্বিতীয়বার সেখানে যেতে পারবেন বলে ভাবতেই পারতেন না। সে সামর্থ্যই ছিল না। তাই সেই পুণ্যিস্থানে প্রিয় সহযাত্রীর সঙ্গে ভগবানকে সাক্ষী মেনে সখ্যের সম্পর্ক পাতিয়ে তীর্থের স্মৃতিটুকু সারাজীবন অক্ষয় করে রাখতেন।
তখনও জগন্নাথের মন্দিরে মহাপ্রসাদ (জগন্নাথের অন্নপ্রসাদ) কিনতে পাওয়া যেত, শুকনো—ছোট্ট ছোট্ট পাশবালিশের মতো দেখতে সুন্দর গোলাপি কাপড়ে সেলাই করা থলিতে। ঠাকুমা আর তাঁর জা, মন্দিরে দাঁড়িয়ে দু'জন-দু'জনের হাতে সেই মহাপ্রসাদ দিয়ে, জিভে ঠেকিয়ে, জগন্নাথকে সামনে রেখে একে-অপরকে ‘মহাপ্রসাদ’ বলে ডেকেছিলেন।
বহুকাল হয়ে গেল, দুজনেই আর নেই। কিন্তু, যতদিন বেঁচে ছিলেন, সেই সখ্যতা তাঁরা বজায় রেখেছিলেন। বার্ধক্যের কারণে ঠাকুমা যখন আর কোথাও যেতে পারতেন না, শুয়ে থাকতেন ঠায় বিছানায়, তখন তাঁর মহাপ্রসাদ রোজ অন্তত একবার ঘোর সাংসারিক আলাপের মাঝে প্রানের কথা বলে হালকা হতে আসতেন, গল্পগুজব করে যেতেন। উৎসব অনুষ্ঠানে পাশে এসে দাঁড়াতেন পরিবারের একজন হয়ে। এঁদের এই সখ্যতা তো আবাল্য নয়, দুই সংসারী মহিলার পড়ন্ত বয়সের সখ্যতা। অথচ, দেখে মনে হত যেন অনাদিকালের মিতালি!
গয়াধামে তীর্থে গিয়ে অনেকেই স্বর্গত পূর্বপুরুষের পিণ্ডদান করে আসেন। পুরনো দিনের অনেকের মুখেই শুনেছি, সেকালে নাকি পিণ্ডদান করতে গিয়ে সধবা মহিলারা সদ্য পরিচিত কারও সঙ্গে ‘গয়াবালি’ নামের সই পাতাতেন। গয়ার ফলগু নদীর বালি হাতে নিয়ে, এ-ওঁর হাতে নতুন নোয়া পরিয়ে, রঙিন সুতোর ডুরি বেঁধে দিয়ে বন্ধুত্বের শপথ নিতেন। কামনা করতেন একে-অপরের আমরণ সধবা জীবন। এখানে শুধু এটুকু ভেবেই আশ্চর্য হই যে, মানুষ যে-ভূমিতে বসে পিণ্ড দিয়ে তার পূর্বপুরুষের সঙ্গে সমস্ত ঐহিক যোগের অবসান ঘটাতে যায়, সেখানেই এক নতুন সম্পর্কের সূচনা ঘটিয়ে এঁরা ফিরে আসতেন ঘরে। ভারি অদ্ভূত, না?
 In English
In English