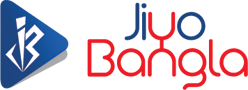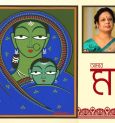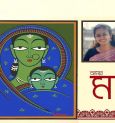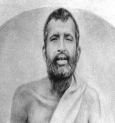কালুরায় বাংলার একজন অনার্য লৌকিক দেবতা। কোনও কোনও মন্দিরে তিন ব্যাঘ্র-দেবদেবী বনবিবি, দক্ষিণরায় ও কালুরায় একসঙ্গে পূজিত হন। কুমিরের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেওয়া হয় কালু রায়ের পূজা। সুন্দরবনে জল ও বনজীবী মানুষেরা তাঁর পুজো করে। অন্যদিকে রাঢ়বঙ্গে পুজো হয় ধর্মরাজ কালু রায়ের। ব্রাহ্মণ লাগে না এই ধর্ম পূজোয়। আগে নাম ছিল কালুরায়। এখন লোকে বলে কালা রায়। অনেক কাল আগে একঘর ডোম পুজোর দায়িত্ব সামলাতো। এখন একঘর জেলে পন্ডিত পূজারী। অনেকটা জমি আছে ধর্মরাজের নামে। সেই জমির লিজের টাকায় বাৎসরিক উৎসব হয়। জেলে বাগ্দী কায়েত সকলে যোগ দেয়।
সুন্দরবনের কালুরায় ও রাঢ়ের ধর্মঠাকুর এক নয়। লোককাহিনি অনুসারে স্থানীয় হিন্দুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে গিয়ে বহুবার হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে পীর বড়খাঁ গাজীর বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটেছে। আঞ্চলিক প্রভুত্বের অধিকার নিয়ে সুন্দরবনের হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে তার প্রবলযুদ্ধ হয়। গাজী ও দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ বিরতির শর্ত অনুযায়ী, কুমির দেবতা কালুরায়কে পুজো করার কথা বলা হয়।
আবার আর এক উপখ্যানে জানা যাচ্ছে যে, কালুরায় মহিষের দেবতা। মেদিনীপুরের বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে এই দেবতার বাস। কিংবদন্তি অনুযায়ী, উত্তরাঞ্চলের উত্তর রায় এবং দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণরায় বড়ভাই কালু রায়ের কাছে মালিকানা সংক্রান্ত বিবাদে হেরে গিয়ে উত্তরে এবং দক্ষিণে পালিয়ে যান। উত্তর রায় সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা। আসলে মানুষ দেবতাদের সৃষ্টি করে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে বা কখনও নিজের ভেতরের ভয় থেকে। মানুষ তার কল্পনা দিয়ে বানিয়ে নেন কত রকমের দেবতা। তাই দেবাদিদেব মহাদেব ভিক্ষুক ব্রাক্ষণ আর আদিশক্তি পার্বতী বাঙালি ঘরের কন্যা হয়ে যান। আকালু রায়ের জন্মের ইতিহাসে লুকিয়ে থাকে অধিকার দখলের বৃত্তান্ত যাকে কোন দৈব বিষয় বলে অন্তত মনে হয় না। মানুষের বশ্যতা মেনে মহিষ মানুষের সাহায্যে বাঘকে হারিয়ে দেয়-তেমনই কালুরায় হারিয়ে দেন দক্ষিণরায়কে।
গ্রামীন মানুষ দক্ষিণরায়ের যেমন আকৃতি দিয়েছে কালু রায়ের তেমন কোন আকৃতি দেয়নি। কোথাও একটি, কোথাও তিনটি, কোথাও আবার পাঁচটি গোলাকার প্রস্তরখন্ড এই দেবতার প্রতীকরূপে অবস্থান করে। তবে কোথাও কোথাও কালুরায়ের মূর্তির খোঁজ মিলছে। দক্ষিণরায়ের মতোই এর মূর্তি একেবারে মানবীয়। পোশাক পৌরাণিক যুদ্ধ-দেবতার মতো। দুই হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, কোমরবন্ধে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ঝোলানো, পিঠে তীর ধনুক। কালুরায়ের মন্দির সেভাবে দেখা যায় না, গাছের তলাতেই তার পূজা হয়। মন্দির খুব কম সংখ্যকেই আছে। কালুরায়ের ডানদিকে থাকে দক্ষিণরায় ও চন্ডী আর বাম দিকে উত্তর রায় ও মঙ্গলাদেবী। কালুরায় অধ্যুষিত এলাকায় যে এক সময় প্রচুর মহিষের আধিক্য ছিল তা এই অঞ্চলের নাম থেকেই জানা যায়। যেমন-মহিষাদল, মহিষগোট প্রভৃতি। পূজামন্ত্ররূপে মহাকাল ভৈরবের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। কারণ মহিষ যমের বাহন, এই দেবতার পূজায় তেমন কোন বাহুল্য নেই। নৈবেদ্য রূপে ফলমূল, কলা, আতপচাল দেওয়া হয়। কালুরায়কে কেন্দ্র করে অনেক কথা কাহিনী লুকিয়ে আছে। তবে একটা ছড়া এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রচলিত-
"উত্তর দক্ষিণরায়ে রাখি দুই পাশে
মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠ কালুরায় বসে।
সবার দক্ষিণে চন্ডী বামেতে মঙ্গলা,
পঞ্চরূপে পৃথিবীতে করেন লীলাখেলা।
কোথা একা, কোথা তিন, কোথা পঞ্চজন
নির্ভয়েতে কালুরায় করেন বিচরণ
ঘরবাড়ি নাহি কিছু বাস বৃক্ষতলে,
সদাচিন্তা কি যে হবে গ্রামের মঙ্গল।
বন্দো কালু রায়ে সবে গ্রামের দেবতা
গ্রামের ভরসা বিপদেতে রক্ষাকর্তা।'
তবে কালুরায় যে শুধু মহিষ বা কুমিরের দেবতা তা নয়। স্থান বিশেষে তিনি ধর্মঠাকুর নামে পূজিত। কালুরায়, বসন্ত রায়, দক্ষিণরায় ইত্যাদি নানা নাম দেবতাটির। ধর্মঠাকুর কেবলমাত্র রাঢ়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রশ্ন জাগে, সে কি তবে রাঢ় অঞ্চল আদিবাসী ও নিম্নবর্গ জাতি অধ্যূষিত অঞ্চল বলে? জলা জঙ্গলের দেবতা কালুরায়, আর রাঢ় অঞ্চলের কালুরায় আলাদা হলেও দুই দেবতা সাধারণ ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় মানুষের দ্বারাই পূজিত হন।
যেমন সুহারি গ্রামের ধর্মঠাকুর কালাচাঁদ বা কালুরায় নামে পরিচিত। মূর্তি কূর্মের। বাহন-সাদা ঘোড়া। জনসাধারণের পূজার পর দুটি পালকিতে সারা গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রামে ঘোরানো হয়। কিন্তু কূর্ম মূর্তি যেহেতু গ্রামের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় না, তাই প্রতীকী কালাচাঁদকে পালকি করে অন্যান্য গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ম হল, যেখানে যেখানে কালাচাঁদের পালকি বাহকরা যাবে বা যেখানে গ্রামের বাইরে পালকি নামাবে, সেখানে সেই পালকিকে আটকানো হবে। গ্রামের লোকেরা নানারকম প্রশ্ন করেন। এ যেন সেই আদিকালের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া আটকানো। তখন যুদ্ধ হত, যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারলে ঘোড়া মুক্তি পেত। এখানে সেটা একটু অন্যরকম, চলে প্রশ্নোত্তরের খেলা। যারা দেবতার পালকিকে আটকে দেন তারা প্রশ্ন করেন। আর সন্ন্যাসীরা, যারা সঙ্গে থাকেন তাদের এর উত্তর দিতে হয়। গ্রাম্য জীবনের এও এক আনন্দের উৎস। প্রথাগতভাবে সেসব যে খুব উচ্চমানের, তা হয়ত নয়। কিন্তু মন্দ লাগে না। গ্রাম্য জীবন, পুরাণ, ইতিহাস, মহাকাব্য অনেক কিছু মিশে আছে এগুলির সঙ্গে। ধর্মরাজ কালু রায়ের পূজার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে গ্রামের মানুষের পালকি আটকে যেসব প্রশ্নোত্তর করা হত, তা উল্লেখ করা যেতেই পারে।
প্রশ্ন—
ফুল সপাটে খেলিরে ভাই ফুলের কর নাম
কোন ফুলেতে তুষ্ট তোমাদের ভোলা মহেশ্বর
কোন ফুলেতে তুষ্ট তোমাদের কৃষ্ণ বলরাম
কোন ফুলেতে তুষ্ট তোমাদের ধর্ম নিরঞ্জন
উত্তর—
ফুল সপাটে খেলি আমরা ফুলের করি নাম
ধুতরো ফুলে তুষ্ট মহেশ্বর
আর কদম ফুলে তুষ্ট কৃষ্ণ বলরাম
আর আকন্দ ফুলে তুষ্ট ধর্ম নিরঞ্জন
এরকম ভাবে সঠিক উত্তর পেলেই পালকি ছেড়ে দেওয়া হত। এরপর নিয়ম মেনে পুজো শুরু হয়। সকালে মন্দির পরিষ্কার করা হয়। স্নান করে মন্দিরে শুদ্ধ কাপড় (পাটের অথবা তসরের, গ্রামে কোথায় কোথায় ছালের কাপড়)পরে মন্দিরে দেবতাকে ঘুম থেকে তোলা হয়(শয়ান থেকে)। সেটি করার জন্য আগে দেহশুদ্ধি করা হয়। তার মন্ত্র শুধু একবার ' নম বিষ্ণু,নম বিষ্ণু'ই যথেষ্ট।
দেহশুদ্ধির পর জাগরণ। তার মন্ত্র—
'যোগনিদ্রা করুন এবার ভঙ্গ, শিব করছে দেখুন রঙ্গ'
এরপর সিংহাসন থেকে পুরনো বাসী ফুল সরিয়ে দেওয়া হয়। সিঁদুর মাখানো হয় মূর্তিকে। সিঁদুর মাখানো হয়ে গেলে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। প্রথমে পুষ্পশুদ্ধ করা হয় তার পর ঠাকুরকে স্নান করানো হয়। বলা হয়-
নম ধর্মরাজ ঠাকুর কালুরায় নমঃ'
এরপর ঠাকুরকে গামছায় মোছানো হয়। মুছিয়ে চন্দনের টিকা পরানো হয়। টিকা পরানোর মন্ত্র আছে, দেবতা কালু রায়ের উদ্দেশ্যে বলা হয়।
সখা পরন্তায় টিকার ফোঁটা পরিলেন কালুরায়
তিনি দেবতায় নমঃ।
কেশবার্থে তৃণমি ত্বং বরদাভব শোভনে
ঠাকুর মালাটিকা পরিছেন, দেখো সবাই। কালুরায় সচন্দন পুষ্প পরিলেন।
ওঁ সন্নিধাং কুরু।
সচন্দন ধর্মরাজ কালুরায় নমঃ। এইবারে দেবতা সিংহাসনে চড়িবেন। ও নমঃ সচন্দন দেবতায় নমঃ। কালুরায় দেবতায় নমঃ।'
এরপর ঠাকুরকে থালা থেকে তুলে সিংহাসনে রাখা হয়। রাখার আগে ফুল দিয়ে সিংহাসন সাজান হয়। পাশে কালাচাঁদ, মহাদেব, দুর্গা ইত্যদিও থাকেন। এরপর নৈবেদ্য সাজিয়ে ধূপ-ধুনো দিয়ে পূজো শুরু। পুজোর মন্ত্র (হাতে আতপচাল নিয়ে)......
'নমঃ কর্তব্য অস্মিন গণপত্রাদি সর্বদেবতা, দেবী গণের পূজা পূর্বকো কালু রায়ের পূজা কর্বানি। ওঁ পূজা করিষ্যামি। নমঃ পূণ্যাহং...নমঃ পূণ্যাহং... নমঃ পূণ্যাহং
উপরোক্ত মন্ত্রগুলি যদি আমরা পড়ি, তাহলে দেখতে পাবো কিভাবে সংষ্কৃত মন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ কথোপকথন টিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। দৈনন্দিন জীবন যাপনের কথাবার্তা,এখানে স্বগতোক্তির মত ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, সমাজ-সংসার সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে পূজার মন্ত্রে।
দুটি বিষয় এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ, নিম্নবর্গ পরিবারের মানুষগুলি দেবতার পূজা,পৌরহিত্য ইত্যাদি থেকে দূরে ছিল বহুদিন, বহুযুগ ধরে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির চাপে সমাজে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। যখন তারা সেই আস্তরণ সরিয়ে সেই অধিকার আবার ফিরে পেতে শুরু করল, ব্রাহ্মণ্য পূজার রীতিগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত করার চেষ্টা করল। কিংবা বলা ভালো, এই রীতিগুলির প্রতি তাদেরও লোভ জন্মাল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অশিক্ষা, ভাষাজ্ঞানের অভাব ইত্যাদি নানাকারণে তা রপ্ত করতে পারল না। ফলও হল মারাত্মক! এগুলি শুনতে, পড়তে আনন্দদায়ক মনে হলেও অজস্র ভুলভ্রান্তিতে ভরা, অনুকরণের একটা অক্ষম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। ভাষা এবং উচ্চারণ দুয়েরই ভুল। মাঝে মাঝেই মন্ত্র ভুলে গিয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপনের কথা উঠে এসেছে। আবার কোথাও কোথাও জনগণকে বোঝানোর জন্য কথ্যভাষার ব্যবহারও করতে হয়েছে পূজার ক্রম ও রীতিগুলি বোঝানোর জন্য। এর পরিণাম হল মানুষ নিজের মত করে এক অধিকার খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেটা হতে পারে কোনও গোঁজামিল কিছুকে পুজো বলে চালিয়ে দেওয়া। তবু তো তারা দেবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে এতেই তাদের আনন্দ। অনার্যদের দেবতা বলা যেতে পারে নিম্নবর্গীয় দেবতা হিসাবে কালুরায় পূজ্য হয়ে উঠেছেন সেই পংক্তির মানুষের হাত ধরেই।
কালু রায়ের প্রসঙ্গক্রমে কালু গাজী নামে এক দেবতার কথাও উঠে আসে, তবে প্রামাণ্য তথ্য হিসাবে যা তথ্য উঠে আসছে তাতে কালুরায় আর গাজী এক নয়। তবে হতে পারে এটি দেবতা কালু রায়ের ইসলামীয় সংস্করণ। তবে মৎস্যজীবী হিন্দুরা এখনও গাজীর নামে পাঠা বলি দেয়! জনশ্রুতি আছে গাজীকালুর আধ্যাত্মিক প্রভাবে বাঘ-কুমিরে একঘাটে জল পান করত।
হিন্দুধর্মালম্বীরা বন দূর্গার বদলে যাদের পূজা করে তাদের মধ্যে গাজী-কালু অন্যতম। তাদের নিয়ে অনেক পৌরাণিক গল্প চালু আছে। রয়েছে কবিতা ও পুঁথি।
বারোবাজার গাজী, কালু,চম্পাবতী'র মাজারে এলে এখানের একটি ফলকে ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস দেখতে পাবেন। গাজী-কালু শুধু দরবেশ ছিলেন না। ইসলাম ধর্ম প্রচারে তার অবদান অনেক! অথচ সেখানের সনাতন ধর্মাবলম্বীরও সমানভাবে মানেন তাদের। কি সুন্দর সাম্যবাদ।
শ্রীরাম রাজার দীঘিটি এখনও আছে। যে কেউ এখানে এলে গাজী-কালু-চম্পাবতী'র মাজার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামরাজার দীঘিটির সৌন্দর্যেও মজবেন। যদিও বর্তমানে এটি বাংলাদেশে। তবে দেবতার ক্ষেত্রে হয়তো ভৌগোলিক সীমারেখা টানা যায় না। বিশেষ করে ভয় যেখানে ভক্তি যোগায়। জল-জঙ্গল, কুমীর-বাঘ নিয়ে যাদের ঘর সংসার করতে হয় সেখানে কালু রায়ের মতো কাল্পনিক শক্তিশালী দেবতার দরকার পড়ে বইকি। সে এপার বাংলা হোক বা ওপার বাংলা। বাংলার লোক সংস্কৃতির মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে তাঁর জন্মের ইতিহাস।
 In English
In English