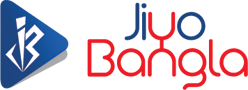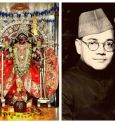বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার হিজরি ১০১৫ বা ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে মহারাজা মান সিংহের সুপারিশে মুঘল দরবার থেকে মজুমদার ও রায়চৌধুরী দুটি উপাধি একসঙ্গে পেয়েছিলেন। ওই একই বছর মান সিংহের সুপারিশে ওই একই উপাধি পেয়েছিলেন নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ ও পাটুলির রাজা জয়ানন্দ। লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের জন্ম ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে। বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় দক্ষ নবাব সরকারের এই কর্মীর মুঘল দরবার থেকে উপাধি পাওয়ার কিছু পরেই তিনি হালিশহরে একটি বিশাল অট্টালিকা তৈরি করেছিলেন। এই জায়গাটি এখন চৌধুরীপাড়া নামে পরিচিত। লক্ষ্মীকান্ত আজকের হালিশহর অর্থাৎ হাবিলী শহরের মাগুরা, খাসপুর বৈকান, আনোয়ারপুর, কলকাতা পরগণা এবং হেতেগড় পরগণার কিছু অংশ জায়গীর হিসেবে পেয়েছিলেন।
সেই সময় মাত্র ১৩০০ টাকায় বিক্রি হয়ে যায় কলকাতা। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কাছ থেকে এই তিনটি গ্রাম কিনে নিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সেই তিনটি গ্রাম নিয়েই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আজকের শহর কলকাতা।
সেদিনের সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের ঘরবাড়ি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। অতীতের নিদর্শন বলতে রয়েছে প্রায় ৩৭০ বছরের পুরনো দুর্গা দালান। আর আটচালার কয়েকটি থাম এবং এই পরিবারের কুলদেবতার রাধাকান্ত জীউয়ের বিগ্রহ। পুরনো বাড়ির শেষ চিহ্ন বলতে ৬৪ সাবর্ণপাড়া রোডের একটি অন্ধকার বাড়ি। যে বাড়ির দেওয়াল প্রায় ৪৫ ইঞ্চি। কলকাতার সবচেয়ে পুরনো বনেদি বাড়ির অস্তিত্ব আজ টিকে রয়েছে এভাবেই।
আজকের কলকাতার বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ অর্থাৎ এই এলাকার লাল দীঘির পাশের কোন এক জায়গায় এই সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের ইটের তৈরি একটি কাছারি বাড়ি ছিল। সঙ্গে শ্যামরায়ের মন্দির। শ্যামরায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে আবির ও কুমকুম সহযোগে হোলি খেলা হত। তারপর সকলের স্নান করত দীঘিতে। দীঘির জল হোলির রঙের লাল হয়ে যেত। সেই থেকে এই দীঘির নাম হয় লালদীঘি। ১৭০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ হওয়ার পর কাছারিবাড়িটি ভেঙে দেওয়া হয়।
জোব চার্ণক বরিশাল সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের ঠাকুরদালান সংলগ্ন আটচালায় বসে কলকাতা কেনার কথাবার্তা স্থির করেছিলেন। ওই পরিবারের বিদ্যাধর রায়চৌধুরী তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। প্রায় ১৬ হাজার টাকা ঘুষ দেওয়া হয়েছিল এই ভবিষ্যতের শহর কেনার জন্য। ঔরঙ্গজেবের নাতি সুলতান আজিম ওসমান তখন বাংলার শাসনকর্তা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নাকি গ্রাম তিনটি কিনেছিলেন রাম রায়, মনোহর দাস ও রায়চৌধুরী পরিবারের অন্য শরীকের কাছ থেকে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা যে কলকাতা বিক্রি করেছিলেন এমন কোন নথি কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। মূল দলিলটি ফারসিতে রচনা করা হয়েছিল। সেখানে যৌথ বিক্রেতা হিসেবে মনোহর দেউ, বিদ্যাধরের ছেলে রামচাঁদ, রামদেবের ছেলে রাম বাহাদুর, প্রাণ এবং গন্ধর্বের নাম রয়েছে।
অনেক ঐতিহাসিকদের মতে এই সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা নাকি গ্রাম তিনটি প্রথমে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন না। আপত্তি জানিয়ে ইংরেজদের নিজেদের মতামত বলেন। কিন্তু সেই আপত্তি ধোপে টেকেনি কারণ আগেই ১৬ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে আজিম ওসমানের ছেলে ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে ইংরেজরা অনুমতি এনেছিলেন। তাই রায়চৌধুরীদের তখন আর কিছু করার ছিল না। ব্রিটিশ শক্তির ক্ষমতা সম্পর্কে রায়চৌধুরীরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা জানতেন ধীরে ধীরে এভাবেই ইংরেজরা ভারতের মূল ভূখণ্ডগুলো নিজেদের আয়ত্তে করে নেবে। তবে তারা এটা আন্দাজ করতে পারেননি এই কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের ওপর এই রাজত্ব শুরু করবে।
বড়িশা নামের উৎপত্তি নিয়েও একটি ইতিহাস প্রচলিত আছে। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭২২ সালে বাংলাকে ১৩টি চাকলা ও বহু পরগণায় বিভক্ত করেছিলেন। সাগর নদীর কেশব রাম রায় চৌধুরী বাংলার দক্ষিণ চাকলায় রাজস্ব আদায় করতেন। সবচেয়ে বেশি রাজস্ব আদায় করতেন বলে বড় রকমের অংশীদারি ছিল তাঁর। বড় হিস্যা সেখান থেকেই কেশব রামের বাসস্থানের নাম হয়েছিল বড়িশা।
সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারে কালীপুজোর চল নেই বলেই শোনা যায়। অথচ এদের পরিবারেরই সম্পত্তি কালীঘাট। একসময় এদের বাড়ি থেকে নৈবেদ্য না গেলে কালীঘাটে পুজো হত না। আজও সাবর্ণদের দুর্গা দালানে প্রতিমা গড়ে সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। তবে এই রায়চৌধুরী পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত হল দুর্গা পুজো। ৩৭০ বছরের পুরনো পুজো। লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরীর আমলে এই পুজো শুরু হয়েছিল। তার আমলে প্রথম যে কাঠামোয় প্রতিমা গড়া হয়েছিল সেই কাঠামোটিতেই আজও প্রতিমা করা হয়। দুর্গা মন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে রাধাকান্ত মন্দির। আটচালায় আসার পথের দুপাশে পড়ে দ্বাদশ শিব মন্দির। রাধাকান্তকে গার্লস হাইস্কুলের দোলমঞ্চে নিয়ে গিয়ে প্রতিবার দোল খেলা হয়। এখানে বসে রাসের মেলা। এই দুর্গা দালান, দোল মঞ্চ, রাসের মেলা আজও একটি বৃহৎ পরিবারের স্মৃতি বয়ে নিয়ে চলে।
 In English
In English