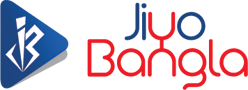পাথর দেখলে বিগ্রহ নেই, বিগ্রহ দেখলে পাথর নেই।
পাথর প্রাণ পেলে হয়ে ওঠে বিগ্রহ। তখন তার আর কঠোরতা থাকে না, বিগ্রহই আনন্দের উৎস, অন্তরে প্রবাহিত হয় রসের ধারা। প্রভু হয়ে ওঠে প্রিয়। তিনি আনন্দময়। বস্তু মাত্রই জীবনময় লক্ষ্য আনন্দ।
সংসার দুঃখ বিশাদ বিষণ্ণতা থেকে উত্তোরণের পঠ দেখিয়েছিলেন তিনি। অন্ধকারে আলো খোঁজাই আনন্দ আ র সে পথেই আসে মুক্তি- এই ছিল তাঁর বার্তা। মানুষ এই পথেই পেয়েছিল আনন্দময়ী মা’কে।
আধ্যাত্মপীঠ ভারতবর্ষ। নানা মত আর পথের দেশ। তবু দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ একদিন চিনেছিল উত্তর-পূর্বে জাত এই আলোক দুহিতাকে।
১৮৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্যের খেওড়া গ্রামে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিতে জন্ম হল এক শিশু কন্যার। কৃষ্ণপক্ষের রাতে জাত সেই নবজাতিকার মুখে কান্না নয়, হাসি দেখেছিল ধাত্রী। নাম দেওয়া হয় নির্মলাসুন্দরী।
যে নির্মল, পবিত্র সেই নির্মলা। যে নির্মলা সেই সুন্দরী।
বাবা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য। মা মোক্ষদাসুন্দরী।

গর্ভাবস্থাতেই নানারকম অলৌকিক ঘটনা ও অধ্যাত্মিক স্বপ্ন দেখতেন মোক্ষদাসুন্দরী। বালিকা নির্মলাসুন্দরী শিশু বয়স থেকেই ঈশ্বরভাবে আকৃষ্ট। কানে হরিনাম গেলেই ভাব সমাধি হয়ে যেত তার। অসাধারণ মেধার অধিকারী। যা একবার পড়তেন গেঁথে যেত মনে।
ইংরেজির ১৯০৮ সালে বারো বছর বয়সে বাংলাদেশের বিক্রমপুরের রমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহ হয়।
ঢাকা জগন্নাথ গঞ্জে রেললাইনের কাছেই রেল কোয়ার্টারে থাকতেন। সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সব কাজের মাঝেও তাঁর মনের ভাবটির কোনও পরিবর্তন হয় না।
জগন্নাথ গঞ্জ থেকে একসময় আসেন স্বামীর কর্মস্থ অষ্টমগ্রামে। তারপর বাজিতপুর। ঘরের কাজে নিপুণা গৃহিণী হলেও মাঝে চলতেই থাকে অলৌকিকের খেলা। সুপ্ত ভাবগুলি ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে। অলৌকিকভাবে দীক্ষা হয় তাঁর। লোকাচার অনুযায়ী নয়। কোনও গুরু দ্বারা নয়। বাংলার ১৩২৯ সালে ঝুলন পূর্ণিমার দিন। স্বতঃস্ফুরিতভাবে।
দেহে দিব্যভাবের প্রকাশ দেখা দেওয়া শুরু করতেই বাক্যহারা হলেন তিনি মৌনভাবে যাপন চলতে লাগে তাঁর।

১৯২৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। বাজিতপুরে অবস্থানের সময় একদিন ভাবের ঘোরে তিনি সিদ্ধশ্বরী মন্দিরের কথা জানিয়েছিলেন। তখনও সেই মন্দির দৃষ্টির বাইরে। পরে যখন খোঁজ পাওয়া যায় সেই মন্দিরের তখন নাকি তা হুবহু মিলে গিয়েছিল তাঁর কথার সঙ্গে। টানা সাতদিন সাতরাত এই মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন তিনি। তারপর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের উত্তর দিকে সাতদিনের মধ্যে একটি ঘর গড়ে দেন তাঁর ভক্তরা। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় বাসন্তী পুজো। পুজো এবং কীর্তনকে কেন্দ্র করে ক্রমশ বিভূতিত প্রকাশ হতে থাকে।
বাজিতপুরের বাসও শেষ হয় একদিন। আনন্দময়ী আসেন ঢাকার শাহবাগে। ক্রমশ তাঁর স্বামীর কাছে তাঁর স্বরূপ উদঘাটিত হতে থাকে। লালপাড় শাড়ি, সিঁদুরের টিপ, কিন্তু অদ্ভুত নিরাসক্ত নির্লিপ্ত উদাসীন চেহারা। এক স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন সারাক্ষণ ঘিরে আছে তাঁকে।
শাহবাগে অবস্থানকালেই শ্রী শ্রী মায়ের মধ্যে দিব্য আকর্ষণী ভাব ফুটে ওঠে। ক্রমশ তা ছ ড়িয়ে পড়তে থাকে মানুষের মধ্যে। স্বামীরমণীমোহন তখন স্ত্রীর কাছেই দীক্ষা পেয়ে হয়ে উঠেছেন ‘ভোলানাথ’। ভোলানাথের অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে সাক্ষাৎও করতেন অনুরাগী মানুষদের সঙ্গে। তবে তারা সংখ্যায় খুবই কম।

ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মাতৃমন্ডলী। মা নির্মলা হয়ে ওঠেন সকলের মা। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ শুরু করেন। ঘরে ফিরলেও বাইরের টান তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ক্রমশ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ন। তাঁর অপার করুণারস আর শান্তির সন্ধান মানুষকে বেঁধে ফেলে তাঁর সঙ্গে। শাহবাগ থেকেই ক্রম হ বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে ‘মা আনন্দময়ী’র নাম। আনন্দময়ী হয়ে সাধারণে ধরা দিলেন তিনি। ‘শাহবাগের মা’ হয়ে ওঠেন শ্রী শ্রী আনন্দময়ী।
হরিদ্বারে গড়ে ওঠে আনন্দময়ী সেবাশ্রম। বহু বিশিষ্ট মানুষ তাঁর কাছে আসতেন। শোনা যায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রী বাসন্তী দেবী। সর্বপরি ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৮১ সালে তিনি তাঁর আশ্রম পরিদর্শন করেন। ১৯৮৭ সালে ভারত সরকার ডাকটিকিৎ প্রকাশ করেন তাঁর।
নিজের বিদায়ক্ষণকেও নিজেই সূচিত করেছিলেন শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী। তিনি ছিলেন রাধারানীর আধার। মহাবিদায়ের দিনটিই বেছে নেন রাধাষ্টমী। ১৯৮২ সালের ২৭ আগস্ট।
তিনি বলেছিলেন, ‘তোমরা তো অভাবের স্বভাবে আছ।তোমরা যা কিছু নিয়ে আছ সবই অস্থায়ী। তাই দুঃখ পাও।যা থাকে না তাই নিয়ে থাকাই হচ্ছে অভাবের স্বভাব।দুখ পাবে না কেন? সুযোগ পেলেই তো মালিক হয়ে বস। মালিক না হয়ে মালী হও। তবেই আর এ সংসারে দুঃখ থাকবে না।’
 In English
In English