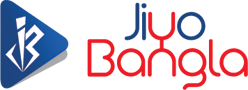চুঁচুড়ার ডাক্তার-কোবরেজের পরিবার, শেকড়-বাকড় ওষুধপাতির সমাহার। তবু, সেই পরিবারে গান ছিল দস্তুরমতো শিরায়-মজ্জায় গেঁড়ে। আর সেই পরিবারেই জন্মেছিলেন বনশ্রী রায়।
বাবা কবিরাজ শৈলেন রায় ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পণ্ডিত মানুষ এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। মেয়ের গলায় সুর আছে দেখে ছোট্ট থেকেই তাকে নিজে তালিম দিতে শুরু করলেন। বাবা ছাড়াও কিছুদিন পর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আর একজন গুণী মানুষ বনশ্রীর গুরু হলেন। তিনি, রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাছে মাসে একদিন ক্লাস। তবে, গানটা যে নিঃশ্বাসের মতোই জীবনে অপরিহার্য, সেটা বাবাই তাঁর অন্তরে বুনে দিয়েছিলেন।
বাবা-কাকা-জ্যাঠা-জেঠি-কাকি-মা-দাদা-ভাই-বোনদের নিয়ে বিরাট একান্নবর্তী পরিবারে সাধে-আহ্লাদে গানে-বাজনায় হৈ হৈ করে দিন কাটতে লাগল বনশ্রীর। কিশোরী বয়সেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলেন বাবার সাহচর্যে। প্রচলিত রেকর্ডের গান, সিনেমার গানও গাইতেন। পাড়ার ফাংশনে আসর মাতাতেন। লোকে তাঁর কণ্ঠে গান শুনে ধন্য ধন্য করত। আর বলত, আহা কী মধুর কণ্ঠ, ঠিক যেন আমাদের সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়! শুনে গর্বে বুক ভরে উঠত বাবার। বাবাকে গর্বিত হতে দেখে আপ্লুত হতেন মেয়েও।
ছন্দ থাকলে ছন্দপতন তো হবেই। বনশ্রীর জীবনেও হল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। একইসঙ্গে পিতা এবং গুরুকে হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখলেন বনশ্রী। ততদিনে সঙ্গীতশিল্পীর জীবনই নিজের ভবিতব্য বলে বরণ করা হয়ে গেছে। সেই ভবিতব্যের পথে আলো দেখিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করার কথা যে গুরুর, তিনিই তো চলে গেলেন অসময়ে! এখন তাহলে কী হবে?
বনশ্রীর দাদাও ডাক্তার। দুষ্যন্ত রায়। তিনিও অসম্ভব গান ভালোবাসতেন, বোনকে তো ভালোবাসতেনই। কাজেই, বোনের অসহায়তা বুঝলেন। বুঝলেন, একান্নবর্তী পরিবারের ভিড়ের মধ্যে বোন এবং বোনের স্বপ্ন যাতে হারিয়ে না-যায়, এমন একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু, চুঁচুড়ার মতো মফঃস্বলে থেকে বোনের জন্য কতটুকু কী করতে পারবেন, বুঝতে পারছিলেন না। এমন সময় তাঁর আলাপ হল গান-পাগল ও অত্যন্ত সজ্জন শান্তি সেনগুপ্ত'র সঙ্গে। ভদ্রলোক সুদর্শন, কলকাতায় থাকেন, পুলিশে চাকরি করেন।
সদ্য যুবতী বনশ্রীর মত নিয়ে শান্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে দিলেন দুষ্যন্ত। বনশ্রী রায় হলেন, বনশ্রী সেনগুপ্ত।
সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গীত জগতের অনেক জ্ঞানীগুণীর আলাপ-পরিচয়। কাজেই তিনি স্বতঃই নিলেন বনশ্রীর নতুন গুরু-অনুসন্ধানের ভার। ভর্তি করে দিলেন সুরকার-গীতিকার-সঙ্গীত শিক্ষক সুধীন দাশগুপ্তর কাছে। সুধীনের ছিল অকৃত্রিম স্নেহের আকর। অচিরেই বনশ্রী হলেন স্নেহধন্য।
সুধীন বনশ্রীর কণ্ঠ থেকে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আবরণ সরিয়ে নিজের কণ্ঠে গাইতে শেখালেন। বনশ্রী তখন থেকে আশা, লতা, আরতি, সন্ধ্যা, হেমন্ত, মান্না-সুধীনের সমস্ত প্রিয় মহিলা ও পুরুষ শিল্পীদের গান নিজস্ব কণ্ঠে নিজস্ব ভঙ্গিতে গাইতে লাগলেন।
শিল্পী হিসেবে বনশ্রীর যাতে নাম হয়, খ্যাতি আসে তার জন্য স্বামীর প্রচেষ্টারও অন্ত রইল না। ফাংশান অর্গানাইজারদের কাছে গিয়ে গিয়ে অনুরোধ জানাতে লাগলেন বনশ্রীকে দলে নেওয়ার জন্য। অনুরোধে তখন কাজ হত। হলও। ফলে, শহর ও শহরের বাইরের নানান ফাংশান-জলসায় গান গাওয়ার সুযোগ পেতে লাগলেন বনশ্রী।
সোনারপুরে একবার একটি ফাংশানে চোখে পড়ে গেলেন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের। সেকালে বিখ্যাত শিল্পীরা নতুনদের গান শুনতেন, ফাংশান শেষ হওয়া অব্দি থাকতেন, নিজেদের গানটুকু গেয়ে পালিয়ে আসতেন না। তা, ধনঞ্জয় দেখলেন বনশ্রীর কণ্ঠ অসাধারণ, অথচ নিজের গান না-গেয়ে হালের বিখ্যাত শিল্পীদের গান গাইছেন!
গান শেষে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ফাংশানে নিজের গান না-গেয়ে অন্যের গান গাইলে কেন? বনশ্রী অসহায় খেদে জানালেন, আমার নিজের কোন গান তো নেই দাদা! কথাটার মধ্যে শুধু অসহায়তা ছিল না, খেদ ছিল না; ব্যথাও ছিল। ধনঞ্জয় সেই ব্যথা বুঝলেন।
ব্যস, দুয়ার খুলে গেল। খুলে দিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। এইচএমভি'র সন্তোষ সেনগুপ্তের নামে খস খস করে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিটি বনশ্রীর হাতে দিয়ে বললেন এইচএমভি'র নলিনী সরকার স্ট্রিটের অফিসে গিয়ে সন্তোষ সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে। বনশ্রী গেলেন। দেখা করলেন। এই এক চিঠিতেই অডিশন হল। সিলেক্ট হলেন। রেকর্ডে গান গাইবার সুযোগ পেলেন। নিজের গান হল। প্রথম রেকর্ডেই খুব নাম হল।
তারপর কেটে গেল একটি একটি করে কয়েকটি দশক। এই সময়কালে 'আজ বিকেলের ডাকে তোমার চিঠি পেলাম', 'ছিঃ ছিঃ এ কি কাণ্ড করেছি', 'আমার অঙ্গে জ্বলে রং মশাল', 'অন্ধকারকে ভয় করি'র মতো কালজয়ী গানগুলো গেয়ে ধীরে ধীরে বাঙালির স্বর্ণযুগের প্রিয়শিল্পীর তালিকায় নিজস্ব একটি জায়গা করে নিলেন বনশ্রী। তাঁর এই 'নিজস্ব জায়গাটি' কোনদিন বিস্মৃতির পাতায় হারিয়ে যাবে না। কারণ, তাঁর এই গানগুলো চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে বাঙালির আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে চিরসবুজ হয়ে এমনভাবে জড়িয়ে রয়েছে যে, তা কোনদিন ভুলে যাবার নয়, হারিয়ে যাবার নয়...
 In English
In English