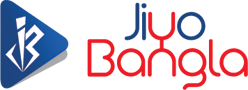অঙ্কে মোটেই ভালো ছিলেন না চিত্তরঞ্জন দাশ। এমনকি পরীক্ষাগুলোতেও খুব একটা ভালো রেজাল্ট তাঁর হত না। ১৮৯০ সালে কম নম্বরের জন্য তাঁর অনার্স সম্পূর্ণ হয়নি, সাধারণভাবে বি এ পাশ করেন। তাই তিনি মজা করে বলতেনও যে, ‘আমি অকৃতকার্যে প্রথম’। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সাধারণ হলেও তিনি কিন্তু দেশের মানুষের কাছে সততার পরীক্ষায় প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন বারে বারে।
বাবা ভুবনমোহন চিত্তরঞ্জনকে বিলেত পাঠালেন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য। যথারীতি চিত্তরঞ্জন সে-পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। হয়তো পাশ করার তেমন তাগিদও তাঁর ছিল না। কারণ, মনটা অনেক আগে থেকেই ইংরেজের গোলামী করতে চাইছিল না। শুধু বাবার কথা কাটতে না-পেরে পড়তে আসা। এইরকম অবস্থায় তিনি স্বাধীন জীবিকাযাপনের জন্য ব্যারিস্টারি পড়াই স্থির করলেন।
ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৯৩ সালে যখন তিনি দেশে ফিরলেন, তখন বাবা ঋণে একেবারে জর্জরিত। সেই ঋণের দায়ে বাবাকে কোর্টে পর্যন্ত যেতে হল। বাড়িতে এমন অনটন শুরু হল যে, সংসার চালানোই কঠিন হয়ে দাঁড়াল। ব্যারিস্টারি পড়ে এসে কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেও পসার জমতে তো সময় লাগে, তাই প্রায় রোজগারহীন চিত্তরঞ্জনের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হল না বিপুল ঋণভার মিটিয়ে বাবাকে দায়মুক্ত করা। তবে সেই দায় থেকে বাবাকে সাময়িক মুক্তি দিতে তিনি বাবা ও নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করলেন। আইনের ফাঁকে বাবাকে দায়মুক্ত করলেও চিত্তরঞ্জন ঋণদাতাদের কিন্তু সত্যি সত্যিই ফাঁকি দিলেন না। কিছুদিন পর থেকে তাঁর যেমন যেমন রোজগার হতে লাগল, তা থেকে ধীরে ধীরে ঋণের পাইপয়সা অব্দি শোধ করে দিতে লাগলেন। বাবার দায় মাথায় নিয়ে তিনি প্রকৃত পুত্রের কর্তব্য পালন করেছিলেন, সেইসঙ্গে পরিচয় দিয়েছিলেন সততারও। তাঁর এই সততা দেখে কলকাতা হাইকোর্টের তখনকার বিচারপতি ফ্লেচার বলেছিলেন যে, ‘দেউলিয়ার খাতায় নাম লিখিয়ে কেউ আবার আগের ঋণ শোধ করে, এমন ঘটনা আমি আগে দেখিনি। এটাই প্রথম।’
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাবার মাথায় বিপুল ঋণভার জমল কী করে? না, বাবার ঋণের পরিমাণ শুধু ছেলেকে বিলেতে পড়তে পাঠানোতে বাড়েনি। বেড়েছে পরের উপকার করতে গিয়ে। বিপদে পড়ে যে যখন এসে তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছে, তিনি অকাতরে তাকে তাই দান করেছেন। এমনকি নিজের হাতে টাকা না থাকলে, ধার করেও দিয়েছেন। অনেকেই সেই উদারতার সুযোগ নিয়েছেন। তারই ফল বিপুল ঋণভার। দানধ্যানে শুধু চিত্তরঞ্জনের বাবাই নন, তাঁর কাকা দুর্গামোহন এবং ঠাকুরদা জগদ্বন্ধুও খুব বিখ্যাত ছিলেন।
শোনা যায়, চিত্তরঞ্জনদের পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের বাড়ির কাছে একটি অতিথিশালা করেছিলেন জগদ্বন্ধু। সেখানে পথচারীরা নিখরচায় থাকা ও খাওয়ার সুবিধে পেত। কিন্তু, অতিথিশালাটি তৈরি করে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না জগদ্বন্ধু। সেখানকার কর্মচারীরা অসহায়-দুর্গত পথচারী অতিথির সেবা ঠিকমতো করছে কি না, তিনি নিয়মিত নিজে পরীক্ষা করে দেখতেন। সেভাবেই একদিন মধ্যরাত্রে নিজে পথচারী সেজে আশ্রয় চাইতে এলেন, কিন্তু আশ্রয় পাওয়া দূরে থাক, কর্মচারীদের কেউ উঠে দরজাটুকু পর্যন্ত খুলল না। তখন তিনি নিজের মূর্তি ধরলেন। তারপর তাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে কর্তব্যকর্ম শিখিয়ে, এমন ভুল আর না-করার তিন সত্য করিয়ে তবে সেখান থেকে গেলেন। আর একবার পালকি নিয়ে পথে যাওয়ার সময় এক অসুস্থ বৃদ্ধকে দেখে নিজে পালকি থেকে নেমে গেলেন; বৃদ্ধকে বাড়ি পৌঁছে দিতে বলে নিজে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। এমনই উদার, সহৃদয় ও পরোপকারীর বংশে জন্ম নিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। ফলে, তাঁর পক্ষে দেশের মানুষের কাছের লোক হয়ে ওঠা, দেশের মানুষের বন্ধু, ‘দেশবন্ধু’ হয়ে ওঠা স্বাভাবিকই ছিল বলা যায়।
দেশের বাড়ি পূর্ববঙ্গে হলেও, কর্মসূত্রে কলকাতার পটলডাঙা স্ট্রিটে বাসা নিয়ে সস্ত্রীক থাকতেন ভুবনমোহন। ১৮৭০ সালের ৫ নভেম্বর এখানেই জন্ম হয় চিত্তরঞ্জনের। পরে তাঁরা ভবানীপুরে উঠে যান। সেখানেই চিত্তরঞ্জনের ছেলেবেলা ও বড়বেলা কেটেছে। বাপঠাকুরদার পরোপকারের ঐতিহ্য চিত্তরঞ্জনের রক্তে ছিল। তাই যখন ব্যারিস্টারিতে খ্যাতি এলো, তখনও নিজের ভোগের জন্য অর্থ জমাতে তাঁর মন চায়নি। বিনাপয়সায় অন্যের জন্য অজস্রবার কেস লড়েছেন। সাহায্য চেয়ে কেউ তাঁর কাছে হাত পেতে দাঁড়ালে তিনি কাউকে কখনই ফিরিয়ে দেননি। এমনকি বিরুদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদককেও না। পুরুলিয়ায় তাঁদের একটি বাড়ি ছিল। সেখানে অনাথ-আতুরদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বেচ্ছায় সেখানকার আশ্রিত অনাথ-আতুরদের সেবার ভার নিয়েছিলেন বোন অমলা দাশগুপ্ত। তিনি নিজের হাতে তাদের পায়খানাপেচ্ছাব পরিস্কার থেকে শুরু করে সমস্ত কাজই করতেন। আর মাসে মাসে বিপুল অঙ্কের খরচ যোগাতেন একা চিত্তরঞ্জন।
অমলা দাশগুপ্ত ছিলেন সুগায়িকা। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন ছিলেন সুলেখক। ফলে, ভাইবোন দুজনেই নিজ নিজ গুণে হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয়। অমলার আবদারে তাঁর জন্য অনেক গান লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথকে ‘রবিবাবু’ বললেও, কবিপত্নীকে বলতেন, 'বৌঠান'। বউঠানের হাতের লুচি আলুরদম ছিল তাঁর খুব প্রিয়। তারই টানে তিনি হাইকোর্ট থেকে আগে সোজা ছুটতেন জোড়াসাঁকো, তারপর পেটপুরে খেয়ে নিজের লেখা রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়ে আর রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখা শুনে তবে ভবানীপুরের বাড়িতে ফিরতেন। এটাই ছিল তাঁর নিত্যনিমিত্তের রুটিন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের তিনি যেমন সখ্যতা পেয়েছেন, অনুজ হয়েও তেমনি পেয়েছেন দানশীলতা ও সততার জন্য শ্রদ্ধা। তাই তাঁর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ হৃদয় উজাড় করে লিখেছিলেন--
'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'
 In English
In English