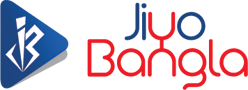বাংলায় কৃষ্ণ আর কালী মিশে একাকার হয়েছে, একবার নয় বহুবার। কৃষ্ণ ও কালীর সেই মিলনের সাক্ষী হুগলি। হুগলিতে কালী হয়ে উঠেছেন বৈষ্ণবী। আবার রঘু ডাকাতও রটন্তী কালীর আরাধনা করেছে। আজ অমাবস্যা। দিকে দিকে চলছে রটন্তী কালী পুজো। মাঘ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে এই পুজো হয়। এই তিথির মহাত্ম্য অসীম। শাস্ত্রমতে, এই তিথিতেই শ্রীরাধার স্বামী আয়ান ঘোষ তাঁর স্ত্রীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন। প্রতি যামিনীতে তমাল কদম্বতলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধিকার প্রণয়ের কথা জটিলা-কুটিলাদের মুখে শুনেও বিশ্বাস করেননি আয়ান। শেষ পর্যন্ত মাঘ মাসের এক গাঢ় অন্ধকার রাতে শ্রীরাধা যখন গোপনে প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখনই তাঁর পিছু নেন শাশুড়ি ও ননদ। ততক্ষণে কৃষ্ণের বাঁশির সুরে মুগ্ধ রাধা পৌঁছে গিয়েছেন কুঞ্জবনে। দু'জনের মিলনদৃশ্য দেখে দ্রুত বাড়ি ফিরে আয়ান ঘোষকে সব জানান জটিলা ও কুটিলা। শ্রী রাধিকা কী করছেন, সে খবর তারা আয়নকে এসে দেন। প্রায় জোর করেই তাঁকে নিয়ে আসেন কুঞ্জবনে। এদিকে ধরা পড়ার ভয়ে ততক্ষণে সন্ত্রস্ত রাধা। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে কালীর রূপ ধারণ করেন। আয়ান ঘোষ কুঞ্জবনে পৌঁছে দেখতে পান গাছতলায় বসে রয়েছেন মা কালী। তাঁর পদসেবা করছেন রাধা রাধিকার স্বামী আয়ন ঘোষ এসে দেখেন রাধিকা কালি পুজো করছেন, লোক লজ্জা থেকে রাধাকে বাঁচানোর জন্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কালীর রূপ ধরেন। ওই রূপ কৃষ্ণকালী নামে পরিচিত। এই দৃশ্য দেখে ভাবে বিভোর হয়ে যান শাক্ত আয়ান। ক্রমে রটে যায় এই কথা। আর সেই থেকেই ওই তিথিতে প্রচলন হয় রটন্তী কালীপুজো। রাধিকার কালী পুজোর কথা রটে গিয়েছিল বলে এই তিথিতে কালী পুজোকে রটন্তী কালী পুজো বলা হয়। বাংলার দিকে দিকে এই তিথিতে পুজো হয়।
তেমনই কৃষ্ণ ও কালী মিলে একাকার হয়ে গিয়েছে, হুগলির হরিপালের শ্রীপতিপুরে অধিকারী পরিবারে। সেখানে কৃষ্ণ ও কালী, দুইয়ে মিলে এক হয়ে গিয়েছে। দেবী কালী গলায় কন্ঠি মালা, বৈষ্ণব তিলক আঁকা। পুজোয় কোনরকম বলি নয়, দেবী তৃপ্ত হন বাঁশির সুরে।আজ থেকে ৭০ বছর আগে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বটকৃষ্ণ অধিকারীর তন্ত্রসাথনায় সিদ্ধ হয়েপ্রথম শুরু করেন এই পুজো। এখানে মা পরম বৈষ্ণবী। বটকৃষ্ণ ঠাকুরের পুত্র কালিপদ অধিকারী পণ্ডিত শিবানন্দপুরী পঞ্চমুন্ডের মন্দিরে সাধনা করেন। সারা বছর এই বৈষ্ণব বাড়িতে মা সবুজ কালি পূজিতা হন।
শ্রীপতিপুরে এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন বটকৃষ্ণ অধিকারী। ম্যাট্রিক্স পাস করে তিনি ভিন রাজ্যে চাকরি করতে গেলেন। কিন্তু মা তার ছেলেকে আবারো ডেকে নেয় কাছে। সংসার ধর্ম করার পরেও তন্ত্রসাধনার দিকে আগ্রহ ছিল তার বেশি। একসময় তিনি শ্মশানে সাধনা করতে করতে সিদ্ধি লাভ করেন। এবং স্বপ্নাদেশে মা কালিকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কুলীন বৈষ্ণব পরিবারে তার জন্ম, যে বাড়িতে কেউ তিলক সেবা, রাধা গোবিন্দের নাম না করে জল স্পর্শ করেন না, সেই বৈষ্ণব বাড়িতে কালী পুজো? তৎকালীন সমাজপতিরা বলে উঠলেন নৈব নৈব চ! কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তিনি বাড়িতে কালীর ঘট স্থাপন করলেন।পরে আবার ও স্বপ্ন দেখেন মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠার। কালো বা নীল নয়, শ্যাম ও শ্যামা এক সাথে, এবং কৃষ্ণ ও কালীর আদেশে বটকৃষ্ণ ঠাকুর রটন্তী কালীপুজোর দিন সবুজ গাত্র বর্ণের কালী মাকে প্রতিষ্ঠা করেন।
ডাকাতরাও রটন্তী কালীর আরাধনা করত। ঘন জনবসতিহীন জঙ্গল, দিনের আলোতেও যেখানে যেতে ভয় পান অনেকে। আশে পাশের এলাকার বাসিন্দাদের মুখে মুখে এখনও শোনা যায় বহু হাড়হিম করা কাহিনী। সেখানেই একরত্তি জায়গায় আজও পূজিতা হন রঘু ডাকাতের আরাধ্য রটন্তী কালী। কালিকা তন্ত্রমতে তন্ত্র সাধকদের সাধনস্থল হিসেবে স্বীকৃত এই স্থান। মাঘ চতুর্দশী ও ভুত চতুর্দশীতে মহা আড়ম্বরে পুজো হয় রটন্তী কালীর। শোনা যায়, কার্তিক অমাবস্যাতেই মা কালীর পুজো করত রঘু ডাকাত।
লোকমুখে প্রচলিত, আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ব্রিটিশ পুলিশ নদীয়া থেকে রঘু ডাকাতকে ধরার চেষ্টা শুরু করে। তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে রঘু ডাকাত ও তার দলবল কেতুগ্রামের অট্টহাসের জঙ্গলে ডেরা বেঁধেছিল। এই জঙ্গলেই রঘু ডাকাত কালী আরাধনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে এখান থেকেই বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের পাশ্ববর্তী অঞ্চলে লুটপাঠ চালাত রঘু। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত রঘু ডাকাত। জানা যায়, রটন্তী কালীকে পুজো করে তারপর সে ডাকাতি করতে বেরোত। তখন থেকেই এই দেবী রঘু ডাকাতের কালী বলে পরিচিত। দেবীর পাষাণ মূর্তির ওপর মহিষাসুরমর্দিনীর প্রস্তর মূর্তি রেখে চলে নিত্যসেবা। প্রায় তিরিশ একর ঘন জঙ্গলের মধ্যে রটন্তী কালীর প্রস্তর মূর্তিকে ঘিরে বসে কালী পুজোর আয়োজন। শোনা যায়, এককালে দেবীকে সন্তুষ্ট করতে নরবলি দিত রঘু ডাকাত। আজও সেই হাঁড়িকাঠ রয়েছে। এখন মাঝে মধ্যে ভক্তদের অনুরোধে ছাগ বলি হয়ে থাকে। শোনা যায়, জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে পঞ্চমুন্ডির আসন। জনশ্রুতি রয়েছে, আসনেই বসে নাকি তন্ত্রসাধনা করে গিয়েছেন সাধক বামাক্ষ্যাপা, গিরীশ ঘোষ।
সময় বদলেছে। আজ আর রঘু ডাকাত বা তার দলবল নেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে আচার বিধিও। কিন্তু আজও রটন্তী কালীর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে রঘু ডাকাতের নাম।
হুগলির এক বিশেষ রীতিতে মাতৃ আধারণার কথা বলে যাই। শাক্ত উপাসনার আধার হল দেবী কালিকার আরাধনা। কালী আরাধনার নিয়মরীতি তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা নির্ধারিত, নির্দেশিত। কিন্তু কালীপুজোর রাতে একটু অন্য রকমভাবে কালিকা আরাধনার সাক্ষী থাকে আরামবাগের রতনপুর গ্রামের কালীশঙ্কর সাঁতরা। মায়ের বুকের উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে পুজো করার পাশাপাশি ভাঙা কাঁচের উপরেও নাচতে দেখা যায় তাঁকে। এই পুজো দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান।
হুগলির আরামবাগের রতনপুর গ্রামে রয়েছে বড়মার মন্দির। মায়ের মন্দিরেই থাকেন কালীশঙ্কর। পুজো করলেও তিনি জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ নন। যদিও তাতে কালী সাধনায় কোনও বাধা পড়েনি। পুজোর সময় প্রথা অনুসারে, মন্ত্রপাঠ করেন না তিনি। কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁখের আওয়াজে যখন গমগম করে ওঠে মন্দির চত্বর, তখন প্রতিমার বুকে পা তুলে দেন কাশীশঙ্কর। মন্ত্রের বদলে নিজের তৈরি সুরেই নিজের লেখা গান গেয়ে পুজো সারেন তিনি।
আগেই মাতৃ মূর্তির সামনে ভাঙা কাঁচ ছড়িয়ে রাখেন তিনি। প্রতিমার বুক থেকে পা নামিয়েই ভাঙা কাঁচে পা রাখেন। তারপর ভাঙা কাঁচের টুকরোর উপরেই নাচতে থাকেন কালীশঙ্কর। ভাঙা কাঁচ উপর গড়াগড়িও দেন তিনি। এই দৃশ্য দেখতে আশপাশ থেকে প্রচুর মানুষ এসে ভিড় করেন বড়মার মন্দিরে। এই পুজোকে ঘিরে মেলাও বসত রতনপুরে।
কথিত আছে, ছোটবেলায় কালীশঙ্কর ঠাকুর গড়তেন। সেই ঠাকুর ছোট্ট কালীশঙ্করের তুলনায় আকারে অনেক বড় হত। তখন প্রতিমার বুকের উপর পা দিয়ে উঠে ঠাকুর গড়া শেষ করতেন ছোট্ট কালীশঙ্কর। নিজে পুজোও করতেন। পরিবারের লোকের নিষেধ শোনেননি তিনি। তারপর থেকেই এইভাবে পুজো করে চলেছেন কালীশঙ্কর। এই অদ্ভুত রীতির পুজো দেখতেই অধিকাংশ মানুষ আসেন এই মন্দিরে।
এই মন্দিরের দুটো বৈশিষ্ট। এক হুগলির আরামবাগের রতনপুর গ্রামের বাসিন্দা কালীশঙ্কর অব্রাহ্মণ বাগদী, অব্রাহ্মণ হয়েও তিনি পুজো করেন। দুই, তাঁর পুজো করার অভিনব পদ্ধতি।
হুগলির আরামবাগের রতনপুর গ্রামের এই বড়মার মন্দির আজকের নয়। দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে বড় মার পুজো। গ্রামে স্থায়ী মন্দির রয়েছে। আজও সেখানে পূজিতা হচ্ছেন মা বড় মা।
 In English
In English