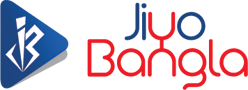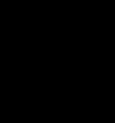মাঘ এক অদ্ভুত সময়। কর্ষণের মহেন্দ্রক্ষণ, শীত আর বসন্তের মিলনক্ষেত্র। পয়লা মাঘ আদপে কৃষি বর্ষের সূচনাকাল। রাঢ়ের কোনও কোনও অংশে মকর পরবের পর এদিন খামার বিশ্রামের দিন। সুবর্ণরেখার অববাহিকায় এদিন হলুদ জলে গরুর পা ধুইয়ে, শিঙে তেল মাখিয়ে, সিঁদুরের ফোটা দিয়ে, নতুন দড়িতে জোয়াল জুতে জমিতে লাঙলা চালাতে হয়। একে হালচার বলা হয়। কোথাও এর নাম 'হাল পুণহা'। ঘর, উঠোনে মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয় পিটুলি গোলা দিয়ে। কর্ষণের সূচনা করেন কৃষক পরিবারের বড় ছেলে। পূর্ব দিকে মুখ করে নিজের খেতে নিজে আড়াই পা লাঙল চালান কৃষক। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে হালপুণহা করা বলে। আড়াই পা লাঙল চালানোর পর বলদগুলিকে পুকুর বা নদীতে স্থান করিয়ে আনা হয়। ধান-দূর্বা-সিঁদুর দিয়ে গরু বা কাড়া দুটিকে বরণ করে নেয় কৃষক-বৌ। সারাদিন উপবাসে থাকার পর সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের শেষে দই-চিড়ে-গুড় খায় কৃষক ও কৃষক-বৌ।
গোবর গর্ত থেকে সারা বছরের গোবর কেটে শুকনো করে জমিতে ছড়ানো হয়। এদিন নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য ভিত কাটা শুরু করাও শুভ। পুরুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে কৃষিবৎসরের সূচনা আখ্যানযাত্রা নামে পরিচিত। পয়লা মাঘ দিনটিতেই আখ্যানযাত্রা হয়। গ্রাম দেবতার থানে লায়া পুজো করতে যান কৃষক। ভাল ফলন কামনায় হাতি, ঘোড়া দিয়ে পুজো দেন। বাঁকুড়ায় বাড়িতে বাড়িতে নিকোনো উঠনে মকর দণ্ড স্থাপন করে ধান্যলক্ষ্মীর পুজো হয়।
এ'সবই কৃষি উৎসব। কিন্তু পয়লা মাঘ তর্পণের দিনও বটে। বাংলাতেও গয়া আছে, তার নাম তেলকুপি গয়া ঘাট। গঙ্গা নয়, ঘাট ছুঁয়ে প্রবাহিত হয়েছে দামোদর। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের তেলকুপি গয়া ঘাটে পয়লা মাঘ পুণ্যস্নান ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন হাজার হাজার আদিবাসী। তর্পণ সেরে মারাংবুরু মন্দিরে তারা পুজোও দেন। মেলা বসে। ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশা থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন।
দামোদরের চরে নাচ-গান করেন, বালির চরেই হয় রান্না। পাত পেড়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্ধ্যায় ফেরার পালা। দামোদর যেন গঙ্গা হয়ে ওঠে একটি দিনের জন্য।
এই দিনে এক অবাক করা মেলার সাক্ষী থাকে সাতগাঁও। বৈষ্ণব সংস্কৃতি মেলাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে। মেলার নেপথ্যে রয়েছে ভগবানের প্রতি ভক্তের ভক্তি, কোথাও সেটা কৃষ্ণপ্রেম, কোথাও শিবের প্রতি ভক্তি কোথাও আবার জগন্নাথের উৎসব। মাঘের পয়লায় হুগলির আদিসপ্তগ্রামের কাছে কৃষ্ণপুর বা কেষ্টপুর গ্রামে ফি বছর যে মেলা হয়, তাও বৈষ্ণব সংস্কৃতির দান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, সে মেলা মাছের।
মেলার বয়স পাঁচশোর বেশি। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে সাতগাঁও এবং পাশ্ববর্তী এলাকার শাসক ছিলেন রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্ধনদাস মজুমদার। হিরণ্যদাস ছিলেন নিঃসন্তান। ১৪৯৮ সালে গোবর্ধনদাসের পুত্র সন্তান জন্মায়। পুত্রের নামকরণ করা হয় রঘুনাথদাস। পুত্রের জন্মের আনন্দে তিনি নির্মাণ করেন কৃষ্ণ মন্দির। এই রঘুনাথদাস হলেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের প্রিয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী।
রঘুনাথ মহাপ্রভুর কৃপাধন্য ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীস্বরূপ দামোদরের কাছে সাধন মার্গে দীক্ষা নিলেন রঘুনাথ। এরপর তিনি পুরী থেকে সপ্তগ্ৰাম ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন মহাপ্রভুর দেওয়া উপহার একটি মদনমোহন বিগ্ৰহ। বিগ্ৰহটি তিনি রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষ্যে সপ্তগ্ৰামে রঘুনাথ দাস এক মহোৎসবের আয়োজন করে। রঘুনাথের ভক্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে ভাত এবং ইলিশ মাছ ও (তখন মাঘ মাস। অসময়ে কাঁচা আম খেতে চাওয়ার উদ্দেশ্যই ছিল পরীক্ষা নেওয়া।) আমের টক খেতে চায় গ্রামবাসীরা। রঘুনাথ সরস্বতী নদী থেকে ইলিশ মাছ ও নিজের আম বাগান থেকে আমের ব্যবস্থা করেন প্রভুর কৃপায়। মন্দিরের পাশে মাঠে বসিয়ে সকল ভক্তদের খাওয়ান। গ্রামবাসী তৃপ্ত হন। এ ঘটনার পর রঘুনাথের নামে ধন্য ধন্য রব ওঠে গোটা কেষ্টপুরে। দিনটা ছিল পয়লা মাঘ।
সেই থেকে শুরু মাছের মেলা। আজও চলছে। মাছের মেলা উত্তরায়ন মেলা নামেও পরিচিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন, আসেন মাছ ব্যবসায়ীরা। পুঁটি থেকে বোয়াল, রুই-কাতলা তো আছেই। মেলায় বিক্রি হয় ভেটকি, পমফ্রেট, চিতল, শংকর, চিংড়ি-সহ নানা ধরণের মাছ। এমনকী কাঁকড়াও! বিকিকিনি চলে। মাছ কিনে, মজে যাওয়া সরস্বতীর তীরে মাছ ভাজা খেয়ে পিকনিক পর্যন্ত হয়। পেল্লাই সাইজের মাছও আনেন বিক্রেতারা। তা দেখতে ভিড় জমে। অন্যদিকে শ্রীপাটে চলে নাম-গান, মহোৎসব।
 In English
In English