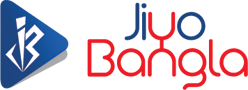শোনা যায়, প্রায় তিন হাজার বছর আগে স্বয়ং সুশ্রুত শবদেহ কেটে শরীরবিদ্যার পাঠ নিয়েছিলেন। তারপর কত যুগ পার হয়ে গেল। আমরা ক্রমশ সংস্কারের পাকে পড়তে পড়তে মড়া কাটা তো দূরের কথা, মড়া ছোঁয়াকে পর্যন্ত অপবিত্র ভাবতে শুরু করলাম। মড়ার গায়ে পড়তে শুরু করলাম তার জাতপাত গোত্র। এই কুসংস্কারের বেড়াজাল ভাঙতেই এগিয়ে এসেছিলেন, এক যুগপুরুষ, তাঁর নাম, মধুসূদন গুপ্ত।
হ্যাঁ, মধুসূদন সত্যই যুগপুরুষ। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন নামকরা বৈদ্য। হুগলির বৈদ্যবাটি তাঁর গ্রাম। সেখানেই জন্ম। ঠাকুরদার বৈদ্য হিসেবে সুখ্যাতি, তাঁর চিকিৎসা নিশ্চিত বালক মধুসূদনকে প্রভাবিত করেছিল; নইলে ১৮২৭ সালে সংস্কৃত কলেজে যখন আয়ুর্বেদ বিভাগ প্রথম খোলা হল যে সাতজন ছাত্রকে নিয়ে, মধুসূদন তাঁদের অন্যতম হবেন কেন!

মধুসূদন রীতিমতো প্রাচ্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। সংস্কৃতভাষায় অসাধারণ বুৎপত্তি, ছন্দ-অলংকার-ব্যাকরণে অসাধারণ দখল। কিন্তু সাহিত্যের বিশারদ হয়ে তিনি বদ্ধ হয়ে গেলেন না। আয়ুর্বেদ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জেগেছিল, তিনি তার সাধনায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সত্যি সাধনা। সাধনা ও মেধার পরিচয় দিয়ে শিক্ষক ক্ষুদিরাম বিশারদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। শিক্ষক অবসর নিলেন। অত্যন্ত যোগ্য ছাত্রকে নিজের জায়গায় অভিষিক্ত করে গেলেন। কিন্তু সহপাঠীরা এক সহপাঠীকে শিক্ষক হিসেবে কিছুতেই মানতে চাইলেন না। প্রতিবাদের ঝড় উঠল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাতে কিছু এলো গেল না। তাঁরা ছাত্রদের প্রতিবাদকে পাত্তাই দিলেন না। মধুসূদনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন। মধুসূদন ছিলেন অন্য স্বভাবের মানুষ। তিনি প্রতিবাদীদের প্রতি বিরূপ না-হয়ে আপন প্রতিভা ও পাঠদানের অপূর্ব পদ্ধতিতে তাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন।
আসলে এই প্রতিবাদ, তিরস্কার, বিরুদ্ধতা—মধুসূদনকে বার বার আঘাত করেও কোনদিন বিপথে চালিত করতে পারেনি। এই যেমন ধরুন, ছেলেবেলায় মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত ডানপিঠে। স্কুলপাঠ্য পড়ার প্রতি ছিল দারুণ অনীহা। আর বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাগী মানুষ। তিনি বার বার ছেলেকে শাসন করেও বাগে আনতে না-পেরে একদিন দিলেন ঘাড় ধরে বাড়ির বাইরে বের করে। ব্যাপারটা মধুসূদনের সম্মানে লাগল। তিনি বাড়ির দরজার দিকে পিছন ঘুরলেন, হাঁটা লাগালেন সোজা কলকাতা। শহরে এসে গাঁয়ের ছেলে গোলোকধাঁধায় পড়ে গোল্লায় যেতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু মধুসূদন সে ফিরিস্তির মধ্যে গেলেন না। বউবাজারে একখানা মাথা গোঁজার ঠাঁই জুটিয়ে একটু কাজের ব্যবস্থা করে নিজের মতো দেদার পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন। বাড়ির লোক বহু কষ্টে বহুদিন পর যখন আঁতিপাঁতি খুঁজে তাঁর সন্ধান পেল, তখন তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়ছেন। তা এ-হেন মানুষকে কোন তিরস্কার, বিরুদ্ধতা, প্রতিবাদ প্যাঁচে ফেলবে!
উনিশ শতকের প্রথমার্ধে, যে সময়ে দাঁড়িয়ে মুক্তদৃষ্টির মানুষ বিরল, সেই সময়েই তাঁর মুক্ত মনের প্রভূত পরিচয় আমরা পাই। এই যেমন ধরুন, যাঁর ঠাকুরদা ছিলেন বিখ্যাত বৈদ্য, যিনি নিজে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিখ্যাত, যাঁকে প্রণম্য শিক্ষক নিজের আসনে বহাল করছেন; অন্য মানুষ তাঁর জায়গায় থাকলে ধরাকে সরাজ্ঞান করতেন। নিজেকে বঙ্গীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে অহং-এর চূড়ান্ত দেখাতেন। কিন্তু মধুসূদন আরও আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রামে গ্রামে রোগী দেখে বেড়াতেন। বিদেশে চিকিৎসা কীভাবে উন্নতি করছে, তার খোঁজ রাখতেন। এটা করতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, চিকিৎসকের কাজ নয় দেশীয় ঐতিহ্যের নামে প্রাচীন পন্থাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা। কেননা, বিজ্ঞান এক জায়গায় আটকে নেই, চিকিৎসা বিজ্ঞানও তাই। চিকিৎসককে তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজনে, রোগ নির্ণয়ে, রুগীকে সঠিক উপায়ে সুস্থ করে তোলার জন্য উদারভাবে সেই অগ্রগতির শরণ নিতেই হবে, তাকে গ্রহণ করতে, প্রয়োগ করতে হবে। আর তার জন্য চাই শরীরবিদ্যার অনুপুঙ্খ জ্ঞান। এই সময় তিনি হুপারের শরীরবিদ্যা বিষয়ে বিখ্যাত বই, ‘অ্যানাটমিস্ট ভেড-ম্যাকাম’ বইটি অনুবাদ করেন। বাংলায় নাম দেন, ‘শরীরবিদ্যা’। এই বই অনুবাদের জন্য তিনি হাজার টাকা পুরস্কার পান।
আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই সময় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। মধুসূদন এই কলেজে শরীরবিদ্যা ও শল্যবিভাগের প্রদর্শক হিসেবে যোগ দিলেন। শল্যবিভাগের চিকিৎসার জন্য দেহের ভেতরের প্রতিটি অঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যক্ষজ্ঞান অত্যন্ত জরুরি। তার জন্য বার বার শবদেহ কেটে সেই জ্ঞানলাভ করতে হয় এবং সেই জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হয়। কিন্তু এ-দেশে জ্যান্ত মানুষের যেমন জাত থাকে, মরার পরও তার বিজাতীয়তা যায় না; সেই মড়া ছুঁলেও সেই সময় জাত যেত। কাটা তো দূরের কথা। প্রথম দিকে, নকল অঙ্গ, পশুদের শরীরের ব্যবচ্ছেদ করে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলল। কিন্তু মানুষের দেহ আর পশুদের দেহের আকার গত ভেতরের অঙ্গের সংস্থানগত অনেক ফারাক রয়েছে। সুতরাং এই বিকল্প পদ্ধতিতে ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই হচ্ছিল না। ফলে, ঠিক হল যে, মানুষের দেহই ব্যবচ্ছেদ করে শিক্ষা দিতে হবে। তথাকথিত ভদ্রলোক যাঁরা, তাঁরা ব্যবচ্ছেদের জন্য দেহ দান করবেন, এ-শিক্ষা সেকালের লোকের ছিল না। তবে ভারতবর্ষে আর যাই থাক, ভাট-ভিখারির বেওয়ারিশ লাশের অভাব আগেও ছিল না, আজও নেই। তারই একটিকে একদিন তোলা হল মেডিক্যাল কলেজের শবকাটা ঘরের টেবিলে। তথাকথিত নীচুজাতের ছাপ মারা, নাম না-জানা এক অস্পৃশ্য দেহ। তাকে ঘিরে উৎসুক সাহেব শিক্ষকেরা। একদিকে সমবেত মেডিকেলছাত্রেরা। হিন্দুসন্তান। ভদ্রবাড়ির সন্তানেরা। তাঁরা ভীত। সমাজের ভয়। সংস্কারের ভয়। জাত যাবার ভয়ে ভীত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র।
দিনটা ১৮৩৬ সালের ১০ জানুয়ারি। ছাত্রেরা কেউ এগিয়ে এলেন না ব্যবচ্ছেদের ছুরি হাতে তুলে নিতে। সাহেব ডাক্তারেরা নানাভাবে তাঁদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাজ হল না। তখন এগিয়ে এলেন স্বয়ং মধুসূদন। নিজের হাতে শবব্যবচ্ছেদ করলেন। তৈরি করলেন ইতিহাস। তিনি আধুনিক ভারতের প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক, যিনি শবব্যবচ্ছেদ করলেন। ছাত্রদের সামনে সমাজের কুসংস্কারকে উপেক্ষা করার প্রেরণা তুলে ধরলেন। দেখালেন, ছেঁদো কুসংস্কারকে পাত্তা দেওয়া বিজ্ঞানের সাধকের কাজ নয়। রক্ষণশীল সমাজের কাজ সমাজ করল। তারা ঘটা করে মধুসূদনকে জাতিচ্যুত করল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করে উঠতে পারল না। কেননা, মধুসূদন তাদের কার্যকলাপকে পাত্তাই দিলেন না। পরের বছর নিজে নেতৃত্ব দিয়ে ষাটটি শব ব্যবচ্ছেদ করলেন।
মধুসূদন সেদিন যেভাবে কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে ভারতের চিকিৎসাশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করেছিলেন, তাতে বাংলার সমস্ত মুক্তমনা মানুষ তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ামে তাঁকে গান-স্যালুট দিয়ে সম্মান জানানো হয়েছিল। এত সম্মান পাওয়ার পরও মধুসূদন পা আপন পথে সামান্য সময়ের জন্যও টলমল করেনি। আধুনিক চিকিৎসা বা এলোপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর ডিগ্রি ছিল না, তিনি নিজে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র হিসেবে যোগ দিয়ে এরপর সেই ডিগ্রি কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন। শবব্যবচ্ছেদ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। প্রচুর বিদেশি চিকিৎসা-গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ১৮৩৬ সালে কলকাতায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়লে, তা প্রশমনের কাজে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কলকাতাবাসীদের বিশুদ্ধ জলসরবরাহ ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এখানকার মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যে কতটা জরুরি এটা তিনিই প্রথম ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরেন। এবং তাঁর পরামর্শকে সম্মান জানিয়ে সরকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেন। সত্যি বলতে কী, একইসঙ্গে প্রশংসা, সম্মান ও প্রতিবন্ধকতাকে কোন আমল না-দিয়ে মাটিতে পা রেখে এভাবে জীবন ও কর্মকাণ্ডের এই মেলবন্ধন, এ যুগপুরুষ না-হলে সম্ভব হয় না।।...
 In English
In English