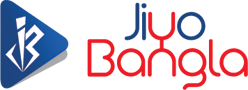স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় শরিক হয়ে ওঠাটা ছিল বীণা দাসের এক অমোঘ ভবিতব্য। কেননা, তাঁর মা সরলা ছিলেন গান্ধিবাদী নীতিতে বিশ্বাসী, অহিংসার পূজারী। ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী। তিনি অনাথ মেয়েদের জন্য ‘পুণ্যাশ্রম’ নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আজীবন চালিয়ে গেছেন। বীণার বাবা বেণীমাধব দাস ছিলেন পেশায় শিক্ষক। তিনি বহু ছাত্রকে দেশের কাজে এগিয়ে আসার কাজে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষের মনে দেশপ্রেমের যে তুফান উঠেছিল, তাতে বেণীমাধবের ভূমিকা অনেকখানি। তিনি সুভাষের মনকে কতটা প্রভাবিত করেছিলেন, তা তাঁকে লেখা সুভাষের একটি চিঠিতে স্পষ্টভাবে ধরা আছেঃ ‘আপনার সঙ্গে আমার যা সম্বন্ধ তা এ জীবনে যাবে না। নইলে নিদ্রায় আপনাকেই স্বপ্নে দেখি কেন? জাগ্রতে আপনার মূর্তি ধ্যান করি কেন?’ বাব-মা ছাড়াও বীণার দুই মামা, আপন দাদা, তুতো-ভাই, দিদি কল্যাণী—এঁরা ছিলেন কোন-না-কোনভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বাড়িতে ছিল সুভাষের প্রায়শ আনাগোনা। ফলে, ছোট থেকেই বেড়ে ওঠার সন্ধিগুলোতে বীণা নানাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দেশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ভাবনায়।
বীণা জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট। তিনি ছিলেন বাড়ির সকলের আদরের। আদর করে সকলে তাঁকে ‘মনু’ বলে ডাকতেন। বীণার যখন দশ বছর বয়স। তখন ভারতের বুকে ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধিজির ডাকে উঠল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। সেই ঢেউয়ের পরশ পেলেন বীণা। মেজদা পড়া ছেড়ে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে জেলে গেলেন। বাবা বাড়িতে চরকা বসালেন। মেয়ের জন্য কিনে আনলেন মোটা খদ্দরের শাড়ি। ফ্রক ছেড়ে সেই প্রথম শাড়ি পরলেন বীণা। এই সময় প্রায়শই বাবা-মা’র কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষের সক্রিয় অংশগ্রহণের নানান কাহিনি শুনতে শুনতে তাঁর মতো দেশের কাজে অংশ নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন বীণা। ঠিক এমনই এক সন্ধিক্ষণে বাড়িতে সুভাষ এলেন, আলাপ হল, সাংঘাতিকভাবে অনুপ্রাণিত হলেন তিনি। ক্লাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিলেনসেই অনুপ্রেরণার স্রোত। সকলে প্রতিজ্ঞা করলেন, ‘দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করব’।
ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় হাতে এল শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ বই। সেই বই বুকের ভেতর আগুন জ্বালাল। বার বার পড়েও যেন আশ মিটতে চাইল না। ওদিকে বইখানা ইংরেজের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হয়ে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। সামনেই পরীক্ষা। ইংরেজির ফার্স্ট পেপারে ‘তোমার প্রিয় উপন্যাস’ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার প্রশ্নে, বীণা ‘পথের দাবী’ নিয়েই লিখে এলেন। বীণা ছাত্রী হিসেবে যেমন ভালো, ইংরেজি ভাষাতেও ছিল তাঁর জব্বর দখল। তবু ‘পথের দাবী’ নিয়ে লেখার দায়ে এই পেপারে নম্বর পেলেন সবচেয়ে কম। তাতে অবশ্য বীণা দমলেন না। বরং একে একে পড়ে ফেললেন ‘নির্বাসিতের আত্মকথা’, ‘কারাকাহিনি’র মতো বিপ্লবীজীবনের আত্মকথামূলক বইগুলি। আর মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন, ‘এমনি জীবন আমাদের হয় না কেন!’
১৯২৮ সাল। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গড়ে তোলা ‘সাইমন কমিশন’-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। দেশময় স্লোগান ওঠে ‘গো ব্যাক সাইমন’। বীণা তখন বেথুন কলেজের ছাত্রী। অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়েন এই আন্দোলনে। আন্দোলনে ঝাঁপ দেন বটে, কিন্তু বুঝতে পারেন না, স্বাধীনতা কোন পথ বেয়ে অর্জন করা যাবে—সহিংস, না অহিংস? সুভাষচন্দ্রের কাছে ঘোচাতে চান সংশয়। সুভাষ বললেন, ‘আসল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্য আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্য আমাদেরও সারা দেশটাকে তেমনি পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠবে না।’ এই কথাতেই বীণার সংশয় ঘুচে গিয়েছিল। তাই বীণার আন্দোলন-জীবনে আমরা সহিংস ও অহিংস পথের অদ্ভুত এক মেলবন্ধন দেখতে পাই। যখন যে আন্দোলন প্রবল হয়ে তাঁর সামনে ধরা দিয়েছে, তিনি তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।
সুভাষের নেতৃত্বে এই সময় বীণা জাতীয় কংগ্রেসে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। শিখতে থাকেন সেনাবাহিনীর অনুশাসন। কিন্তু অস্ত্রহীন সৈন্য হয়ে দিন কাটাতে তাঁর আর ভালো লাগছিল না। তাই পাশাপাশি যোগ দিলেন ‘যুগান্তর’ নামের বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিতে। গুপ্তসমিতিকে অস্ত্র কেনার টাকা জোগাতে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় বেনামে লেখার চেষ্টা করলেন, লটারি বিক্রির কাজ নিলেন, টিউশ্যনি শুরু করলেন। এই সময় দল তাঁকে এবং কমলা দাশগুপ্তাকে দায়িত্ব দিল বাংলার গভর্নর স্যার স্টেনলে জ্যাকসনকে সরিয়ে দেওয়ার। এসে গেল রিভলভার। গুলি চালাবেন বীণা। কিন্তু পরিকল্পনা এত তাড়াতাড়ি হল যে, বীণা নিশানা অভ্যাসের সময় পেলেন না।
১৯৩২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। ইউনিভার্সটি কনভোকেশনে ভাষণ দিতে হাজির হয়েছিলেন স্টেনলে জ্যাকসন। তিনি যখন ভাষণ দিতে উঠলেন, তখন শাড়ির আঁচলের তলায় রিভলভার লুকিয়ে বীণা হাজির হলেন সভায়। আচমকা আড়াল থেকে রিভলভার বার করে ছুঁড়লেন গুলি। কিন্তু অনভ্যাসের জন্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন স্টেনলে জ্যাকসন। আতঙ্কে শুরু হয়ে গেল সভাময় হুড়োহুড়ি চিৎকার। কিন্তু বীণা পালাতে পারলেন না। উপস্থিত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু বীণার কাছ থেকে কোন তথ্য আদায় করতে পারল না। ইংরেজের পুলিশ তাঁর বাবা-মাকে থানায় এনে টোপ দিল। বলল যে, বীণা রিভলভার কোথা পেয়েছেন, এটা বললেই ছেড়ে দেবে। সে-কথা শুনে পুলিশকে ধমকে বীণা বলেন যে, ‘আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না, আমার বাবা মেয়েকে বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।’
হত্যার চেষ্টার দায়ে বিচারে বীণার ন’বছর কারাদণ্ড হল। যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে বীণা বিবাহ করেছিলেন দলের সদস্য সতীশচন্দ্র ভৌমিককে। এই মামলায় ইংরেজের পুলিশ সতীশচন্দ্রকে যুক্ত করে হত্যা-প্রচেষ্টার সহযোগী হিসেবে আদালতে টেনে এনে বার বছরের কারাদণ্ড দেওয়ালো।
গান্ধিজির রাজবন্দি মুক্তি আন্দোলনে মেয়াদের আগেই বীণা কারামুক্ত হলেন। এরপর জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে গান্ধিজির পথেই স্বদেশমুক্তির জন্য লড়াই শুরু করলেন তিনি। ভারত ছাড় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আবার বন্দি হলেন। তিন বছর জেলে কাটিয়ে মুক্ত হয়ে ছুটলেন নোয়াখালী দাঙ্গায় দুর্গত মানুষের সেবার কাজে। এই সময় থেকেই গান্ধিজির অহিংস আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণের সেবায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন তিনি। এলেন সংসদীয় রাজনীতিতে। এই সময় থেকেই কুসংস্কারমুক্ত ও গণতান্ত্রিক সাম্যময় এক সমাজ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের ছবি তাঁকে তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁর সংগ্রামী-স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি। সেই হতাশার জায়গা থেকে তিনি সোচ্চারে বলেছিলেন—‘আমরা কি সত্যিই স্বাধীন হয়েছি? ইট ইজ ওনলি দ্য ট্রান্সফার অব পাওয়ার। নট ফ্রিডম।’
স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণার শেষ জীবন সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। রাজনীতির আলো থেকে সরে গিয়ে বেছে নিয়েছিলেন প্রান্তিক জীবন। স্বাধীন স্বদেশ, স্বাধীন জনতা, রাজনীতির উদ্ভাসিত অঙ্গন—এই বীরাঙ্গনাকে অচিরেই ভুলে গিয়েছিল। তারই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটে পুলিশ পঁচাত্তর বছর বয়সী বীণার মৃতদেহ উদ্ধার করে। সংবাদপত্রে সে-খবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি তখন কেবল ‘অজ্ঞাত পরিচয়’ এক মৃতদেহ। পরে অবশ্য তাঁর পরিচয় জানা যায়। শোরগোল ওঠে। কিন্তু বীণা কীভাবে, কোন অবস্থায় হরিদ্বার গেলেন; সে-সব আর কিছুই জানা যায় না। শুধু তাঁর সেই নিঃসঙ্গ মৃত্যু, মর্মান্তিক পরিণতি বিস্মৃতির আড়াল পেরিয়ে আজও এক কষ্ট জাগায় আমাদের অনেকের আত্মার অন্দরে...
 In English
In English